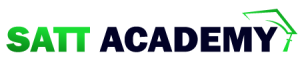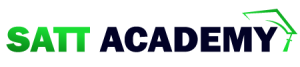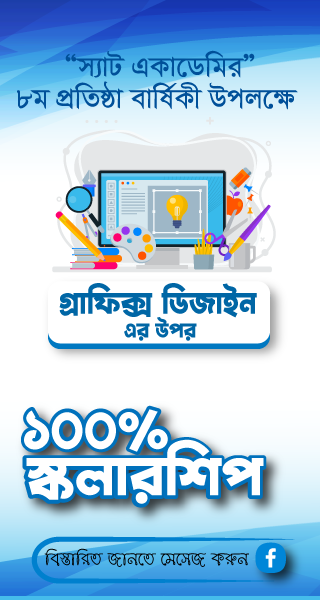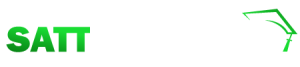পৃথিবীর প্রথম স্তন্যপায়ী প্রাণীর ক্লোন ডলি নামের একটি ভেড়া আধুনিক বংশগতি বিদ্যার (Genetics) ভিত্তি গড়ে উঠেছে আজ থেকে প্রায় ১৫০ বছর পূর্বে গ্রেগর মেন্ডেল নামে একজন অস্ট্রীয় ধর্মজাজকের গবেষণার মাধ্যমে। যেডেলের আবিষ্কারের মূল প্রাতিগাচ্চ হচ্ছে জীবের প্রতিটি বৈশিষ্ট্য এক জোড়া ফ্যাক্টর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বেটসন ১৯০৮ সালে মেন্ডেলের ফ্যাক্টরের নাম দিলেন জিন। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই বংশগতি বিদ্যা নানাভাবে বিকাশ লাভ করতে থাকে। নানা তথ্যে সমৃদ্ধ হতে থাকে এর ভাণ্ডার। বংশগতির একক বা জিনের উপাদানের প্রকৃতি, রাসায়নিক এবং অণুর গঠন ও জৈবনিক প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিগুলো আবিষ্কৃত হওয়ার পর জীববিজ্ঞানীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করলেন, নিষেক ছাড়াই কীভাবে একটা জীবকোষ থেকে জিন আরেকটা জীবকোষে প্রতিস্থাপন করা যায়, সেটি নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক হার্বার্ট বয়ার এবং স্ট্যানলি কোহেন ১৯৭৩ সালে প্রথম নিষেক ছাড়াই কৃত্রিমভাবে জিন সংযোজনে সাফল্য লাভ করেন। জীববিজ্ঞানের ইতিহাসে যেটি ছিল এক অচিন্তনীয় ঘটনা। স্থাপিত হলো জীবপ্রযুক্তি (Biotechnology) নামে জীববিজ্ঞানের নতুন এক শাখা। আমরা এ অধ্যায়ে জীবপ্রযুক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করার পূর্বে ক্রোমোজোম, জিন, ডিএনএ ও আরএনএ সম্বন্ধে আলোচনা করব। এগুলো সম্পর্কে আমরা অষ্টম শ্রেপিতে খানিকটা ধারণা পেয়েছি। এ অধ্যারে বিস্তারিত জানব।
এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা :
- চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বংশপরম্পরায় স্থানান্তরের কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ডিএনএ টেস্টের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- জেনেটিক বিপ্লতার (Genetic Disorder) কারণ ও ফলাফল বর্ণনা করতে পারব।
- জীবপ্রযুক্তি এবং জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রাণী ও উদ্ভিদে ক্লোনিং ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ক্লোনিংয়ের সামাজিক প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ও বায়োটেকনোলজির ব্যবহার এবং এদের সুফল বিশ্লেষণ করতে পাৱৰ ।
কোষ হচ্ছে জীবদেহের একক। যেটি অন্য কোনো সঞ্জীৰ মাধ্যমের সাহায্য ছাড়াই নিজের প্রতিরূপ তৈরি করতে পারে। কোষকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়, এক ধরনের কোষে কোনো সুগঠিত নিউক্লিয়াস থাকে না, অন্য ভাগে সুগঠিত নিউক্লিয়াস (চিত্র ১১.০১) থাকে, এই কোষের নিউক্লিয়াসের ভেতর জীবদেহের জন্য প্রয়োজনীয় অনেক উপাদান থাকে, যার একটি হচ্ছে ক্রোমোজম। প্রতিটি প্রকৃত কোষবিশিষ্ট জীবের নিউক্লিয়াসের নিউক্লিওপ্লাজমে অনেক ক্রোমাটিন ফাইবার বা তন্তু থাকে। কোষের স্বাভাবিক অবস্থার এগুলো নিউক্লিয়াসের ভিতরে বিশৃংখল অবস্থায় থাকে। কোষ বিভাজনের সময় পানি বিয়োজনের ফলে এগুলো স্পন্ট আকার ধারণ করে এবং আকারে এগুলো সুতার মতো হয়। এগুলোকে ক্রোমোজোম (চিত্র ১১.02) বলে। কোষ বিভাজনের সময় প্রোফেজ ও মেটাফেজ দশায় ক্রোমোজোমগুলো স্পষ্ট হয়। প্রতিটি প্রজাতির কোষে ক্রোমোজোমের সংখ্যা সবসময় নির্দিষ্ট। অর্থাৎ একটি প্রজাতির প্রাণী অথবা উদ্ভিদ কোষে যদি ১২টি ক্রোমোজোম থাকে, তাহলে সেই প্রজাতির সকল সদস্যের কোষে সবসময় ক্রোমোজোমের সংখ্যা ১২ থাকবে।
১১.১.১ ক্রোমোজোমের আকৃতি
ক্রোমোজোমের আকার সাধারণত লম্বা। প্রতিটি ক্রোমোজোমের দেহ দুই গুচ্ছ সুতার মতো অংশ নিয়ে গঠিত (চিত্র ১১.০৩)। প্রতিগুচ্ছ সুতার মতো অংশকে ক্রোমোনেমা (বহুবচনে ক্রোমোনেমাটা) বলে। কোষ বিভাজনের সময় প্রতিটি ক্রোমোজোম সমান দুভাগে ভাগ হয়ে যায়। এদের প্রতিটিকে ক্রোমাটিড বলে। প্রতিটি ক্রোমাটিড একটি ক্রোমোনেমা নিয়ে গঠিত।বর্তমানে কোষতত্ত্ববিদরা বলেন ক্রোমাটিড ও ক্রোমোনেমা ক্রোমোজোমের একই অংশের দুটি নাম। মাইটোসিস কোষ বিভাজনের মেটাফেজ দশায় প্রত্যেকটি ক্রোমোজোমে যে ধাত্র গোলাকৃতি ও সংকুচিত স্থান দেখা যায়, তার নাম সেন্ট্রোমিয়ার। অনেকে আবার একে কাইনেটোকোরও বলে। ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ারের উভয় পার্শ্বের অংশকে বাহু বলা হয়। পূর্বে ধারণা করা হতো ক্রোমোজোম একটা মাতৃকা বা ধাত্র দ্বারা আবৃত। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এটি কিছু প্রোটিন ও অজৈব পদার্থের সমাবেশ, যা ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ ছাড়া দেখা যায় না।
চিত্র ১১.০২: ক্রোমোজোম
ক্রোমোজোমের প্রকারভেদ
উচ্চ শ্রেণির প্রাণী বা উদ্ভিদের কোষের ক্রোমোজোমের মধ্যে প্রকারভেদ দেখা যায়। এদের দেহকোষে যতগুলো ক্রোমোজোম থাকে, তাদের মধ্যে এক জোড়া ক্রোমোজোম অন্যান্য ক্রোমোজোম থেকে ভিন্নধর্মী। এই ভিন্নধর্মী ক্রোমোজোমকে সেক্স ক্রোমোজোম বলা হয়। বাকি ক্রোমোজোমগুলোকে অটোজোম (Autosorne) বলা হয়। সেক্স ক্রোমোজোমগুলোকে সাধারণত X ও Y নামে নামকরণ করা হয়ে থাকে। তোমরা এর মাঝে আগের অধ্যারে দেখে এসেছ যে মানুষের প্রতিটি দেহকোষে ২৩ জোড়া ক্রোমোজোম আছে এর মাঝে ২২ জোড়া অটোজোম এবং এক জোড়া সেক্স ক্রোমোজোম।
১১.১.২ ক্রোমোজোমের রাসায়নিক গঠন
ক্রোমোজোমের রাসায়নিক গঠনে দেখা যায় এর মধ্যে রয়েছে নিউক্লিক এসিড, প্রোটিন এবং অন্যান্য উপাদান ।
নিউক্লিক এসিড: নিউক্লিক এসিড দুই ধরনের হয়, (ক) ডিএনএ বা ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড (DNA) এবং (খ) আরএনএ বা রাইবোনিউক্লিক এসিড (RNA)।
ডিএনএ (DNA)
ডিএনএ-এর পূর্ণ নাম ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড। ডিএনএ সকল জীবের আদি বস্তু এবং জীবকোষের নিউক্লিয়াসের সকল ক্রোমোজোমে এর অবস্থান রয়েছে। এ তথ্যটি উদঘাটিত হওয়ার পর বিজ্ঞানীরা ডিএনএর পাঠনিক উপাদান জানার কাজে সচেষ্ট হলেন। ১৯৫৩ সালে জেমস ওয়াটসন ও ফ্রানসিস ক্লিক ডিএনএ অণুর পঠন বের করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই যুগান্তকারী পেয়েছিলেন। তারা দেখিয়েছিলেন যে ডিএনএ অণু আসলে দুটি সুতার মতো লম্বা নিউক্লিওটাইডের (চিত্র ১১.০৪) শেকল বা পলিনিউক্লিওটাইড। প্রতিটি নিউক্লিওটাইডে রয়েছে একটি করে পাঁচ কার্বনের রাইজোম শর্করা। একটি ফসফেট এবং নাইট্রোজেন ক্ষারক। ডিএনএ অণুর আকৃতি প্যাঁচানো সিঁড়ির মতো (চিত্র ১১.০৫)। প্যাঁচানো সিঁড়ির দুপার্শ্বের মূল কাঠামো গঠিত হয় নিউক্লিওটাইডের পাঁচ কার্বন যুক্ত শর্করা এবং ফসফেট দিয়ে। শর্করা ফসফেটের কাঠামোটি বাইরের কাঠামো। ভেতরে নিউক্লিওটাইডগুলো যুক্ত থাকে নাইট্রোজেনের ক্ষারক দিয়ে। চার ধরনের নাইট্রোজেন ক্ষারকের মধ্যে দুটি করে ক্ষার জোড় বেঁধে তৈরি করে সিঁড়ির ধাপগুলো। ডিএনএ অণুর চার ধরনের ক্ষারক হচ্ছে এডিনিন (A), গুয়ানিন (G), সাইটোসিন (C) ও থাইমিন (T)-এর মাঝে এডিনিন সবসময় থাইমিনের সাথে (A-T) এবং সাইটোসিন সবসময় গুয়ানিনের সাথে (C-G) জোড়া বাঁধে। ডিএনএ প্যাঁচানো সিঁড়ির মতো কাঠামোকে ডাবল হেলিক্স বলা হয়ে থাকে।
আরএনএ (RNA)
আরএনএ হলো রাইবোনিউক্লিক এসিড (চিত্র ১১.০৬)। DNA-এর মতো দুটি শেকলের বদলে এটি একটিমাত্র পলিনিউক্লিওটাইড শেকলে ভাঁজ হয়ে থাকে। আরএনএ পাঁচ কার্বন যুক্ত রাইবোজ শর্করা ও ফসফেট নির্মিত একটি মাত্র পার্শ্ব কাঠামো দ্বারা গঠিত, যার ডিএনএর মতোই চার ধরনের নাইট্রোজেন ক্ষারক রয়েছে । শুধু পার্থক্য হচ্ছে ডিএনএতে থাইমিন আছে, কিন্তু আরএনএ-তে থাইমিনের পরিবর্তে থাকে ইউরাসিল (U)। জীবকোষে আরএনএ তিন রকমের। সেগুলো হচ্ছে: (ক) বার্তা বাহক আরএনএ (Messenger RNA বা mRNA), (খ) রাইবোজোমাল আরএনএ (Ribosomal RNA বা rRNA) এবং (গ) ট্রান্সফার আরএনএ (Transfer RNA বা t RNA)।
প্রোটিন
ক্রোমোজোমে দুই ধরনের প্রোটিন থাকে। সেগুলো হচ্ছে-হিস্টোন ও নন-হিস্টোন প্রোটিন। ওপরের বর্ণিত রাসায়নিক পদার্থগুলো ছাড়া ক্রোমোজোমে লিপিড, ক্যালসিয়াম, আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম আनন ও অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ অল্প পরিমাণে পাওয়া যায়।
১১.১.৩ জিন
অষ্টম শ্রেণিতে দ্বিতীয় অধ্যায় এ আমরা বংশগতি বলতে কী বুঝায় সেটা জেনেছি। বংশগতিতে ক্রোমোজোমের কী ভূমিকা আমরা সেটাও জেনে এসেছি। মেন্ডেল বংশগতির ধারক এবং বংশপত বৈশিষ্ট্যের নির্ধারকের একককে ফ্যাক্টর নামে আখ্যায়িত করেছিলেন এবং বলেছিলেন ফ্যাক্টরগুলোর মাধ্যমে পিতামাতার বৈশিষ্ট্যগুলো বংশপরম্পরায় সন্তানদের মাঝে বাহিত হয়। বর্তমানে বংশগতি বিদ্যার অগ্রগতির ফলে বংশগতির কৌশল সম্বন্ধে আরও অনেক জ্ঞান অর্জিত হয়েছে। মটরশুঁটি ছাড়াও অন্যান্য জীবের বংশানুগতির পদ্ধতি নিয়ে এর পর ব্যাপক গবেষণা শুরু হয়। বেটসন ১৯০৮ সালে মেন্ডেলের ফ্যাক্টরের নামের পরিবর্তে জিনেটিক শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। ১৯০৯ সালে জোহানসেন বংশপরম্পরায় কোনো বৈশিষ্ট্যের নির্ধারক একককে আরো সংক্ষেপে জিন নামকরণ করেন। ক্রোমোজোমের ভেতর ডিএনএ র যে দীর্ঘ “শেকল” রয়েছে, তার একটি অংশে বংশগতির কোনো একটি একক লিপিবদ্ধ থাকে সেটিকে বলা হয় জিন। ক্রোমোজোমের গায়েই সন্নিবেশিত থাকে অসংখ্য জিন বা বংশগতির একক। জীবজন্তুর বৈচিত্র্যের নিয়ন্ত্রক হচ্ছে জিন। এককোষী ব্যাকটেরিয়া, আমাশয় রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু অ্যামিবা থেকে শুরু করে বিশাল আকৃতির বটবৃক্ষ, বিশাল আকৃতির হাতি, তিমি ইত্যাদি বুদ্ধিমান জীব মানুষ পর্যন্ত সবারই আকৃতি প্রকৃতি নির্ধারিত হয় তার জিনের সংকেত দ্বারা।
বংশবৃদ্ধির প্রয়োজনে প্রতিটা জীব তার অনুরূপ জীবের জন্ম দেয়। এসবই জিনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এভেরি, ম্যাকলিওড এবং ম্যাককারটি (১৯৪৪) মানুষের নিউমোনিয়া রোগ সৃষ্টিকারী নিউমোকক্কাস ব্যাকটেরিয়ার রাসায়নিক গঠন যেমন- প্রোটিন, শর্করা, ফ্যাট এবং নিউক্লিক এসিডগুলো পৃথক করেছিলেন। প্রত্যেকটি উপাদান নিয়ে পৃথকভাবে পরীক্ষার মাধ্যমে তাঁরা নিশ্চিত হলেন যে শুধু ডিএনএ বংশগত বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণের সাথে সম্পর্কিত। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ডিএনএ কীভাবে বংশগত বৈশিষ্ট্যগুলোকে পরবর্তী বংশে সঞ্চালিত করে? ছবিতে একটি ডিএনএ কীভাবে দুটি ডিএনএতে বিভাজিত হয় দেখানো হয়েছে। প্রথমে ডিএনএ শেকল লম্বালম্বিভাবে স্ববিভাজনের (Self duplication) দ্বারা ভাগ হয়ে পরিপূরক দুটি পার্শ্ব কাঠামো গঠিত হয়। তখন কোষের মাঝে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা A, T, C এবং G ক্ষারকগুলো ডিএনএ র উন্মুক্ত A, T, C এবং G সাথে যুক্ত হয়। সব সময়ই A-এর সাথে T এবং C-এর সঙ্গে G যুক্ত হয় বলে একটি ডিএনএ অণু ভেঙে তৈরি হয় দুটি নতুন অণু। নতুনভাবে সৃষ্ট প্রতিটা অণুতে থাকে একটা পুরাতন ও একটা নতুন ডিএনএ পার্শ্ব কাঠামো, যার ফলে প্রতিটি নতুন ডিএনএ অণু হয় মূলটির হুবহু অণুলিপি। এভাবে ডিএনএ অণুতে রক্ষিত জীবের বংশগত বৈশিষ্ট্যের সাংকেতিক নীলনকশা পরিবর্তন ছাড়াই সংরক্ষিত হয় এবং পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়।
অতএব তোমরা বুঝতে পারছ বংশগত ধারা পরিবহনে ক্রোমোজোম, ডিএনএ কিংবা আরএনএ র গুরুত্ব অপরিসীম। ক্রোমোজোমের প্রধান উপাদান হচ্ছে ডিএনএ। ডিএনএ র অংশ বিশেষ জীবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রকৃত ধারক, যাকে জিন বলা হয়। আরএনএ জীবের বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করতে ডিএনএ-কে সাহায্য করে। ক্রোমোজোম ডিএনএ এবং আরএনকে ধারণ করে বাহক হিসাবে। ক্রোমোজোম ডিএনএ, আরএনএ-কে সরাসরি বহন করে পিতা-মাতা থেকে তাদের পরবর্তী বংশধরের মাঝে নিয়ে যায়। কোষ বিভাজনের মায়োসিস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বংশগতির এ ধারা অব্যাহত থাকে। এ কারণে ক্রোমোজোমকে বংশগতির ভৌত ভিত্তি বলে আখ্যায়িত করা হয়।
ডিএনএ টেস্ট
যখন কোনো সন্তানের পিতৃত্ব বা মাতৃত্ব নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হয় অথবা কেউ যদি কোনো সন্তানকে তার সন্তান হিসেবে দাবি করে, তখন ডিএনএ টেস্ট দ্বারা এ ধরনের বিবাদ নিষ্পত্তি করা যায়। ডিএনএ টেস্ট করার সময় পিতা, মাতা ও সন্তানের শরীর থেকে কোনো ধরনের জীবকোষ (রক্ত, লালা ইত্যাদি) সংগ্রহ করা হয়। সেখান থেকে নানা ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়ার দ্বারা পিতা, মাতা ও সন্তানের ডিএনএ র একটি চিত্র (প্রোফাইল) প্রস্তুত করা হয়। এরপর সন্তানের ডিএনএ র চিত্রের সাথে পিতামাতার ডিএনএ চিত্র মিলানো হয় এবং যদি প্রত্যেকের সাথে প্রায় ৫০% মিল পাওয়া যায়, তাহলে সে সেই সন্তানের জৈব পিতামাতা (Biological Parents) অর্থাৎ প্রকৃত পিতামাতা হিসাবে গণ্য করা হয় ।
১১.১.৪ মানুষের জেনেটিক বিশৃংখলা
চিকিৎসাবিজ্ঞানে মানুষের জেনেটিক বিশৃংখলার কারণে সৃষ্ট রোগগুলো একটি অনেক বড় উদ্বেগের বিষয়। এ রোগগুলো কীভাবে মাতাপিতা থেকে সন্তানদের মধ্যে সঞ্চালিত হয় এবং কী ধরনের জেনেটিক বিশৃংখলার কারণে রোগগুলো ঘটে— এগুলো বিজ্ঞানীরা বুঝতে শুরু করেছেন। নিম্নলিখিত কারণে এ রোগগুলো ঘটতে পারে-
১. পয়েন্ট মিউটেশন বা জিনের ভিতর পরিবর্তনের জন্য
২. ক্রোমোজোম সংখ্যার হ্রাস বা বৃদ্ধির জন্য
৩. ক্রোমোজোমের কোনো অংশের হ্রাস বা বৃদ্ধির জন্য
৪. মায়োসিস কোষ বিভাজনের সময় হোমোলোগাস (মা থেকে পাওয়া একটি এবং বাবার কাছ থেকে পাওয়া আরেকটি ক্রোমোজোমের জোড়া) ক্রোমোজোমের বিচ্ছিন্নকরণ (Non-disjuntion) না ঘটার জন্য। এই কারণগুলোর জন্য মানুষের যে বংশগত রোগগুলো সৃষ্টি হয় তার কয়েকটা নিচে উল্লেখ করা হলো:
১. সিকিল সেল (Sickle cell): মানুষের রক্ত কণিকার এ রোগটি হয় পয়েন্ট মিউটেশনের ফলে। স্বাভাবিক লোহিত রক্ত কণিকাগুলোর আকৃতি চ্যাপ্টা। কিন্তু সিকিল সেলের ক্ষেত্রে লোহিত কণিকাগুলোর আকৃতি কিছুটা কাস্তের মতো হয়। সিকিল সেলগুলো সূক্ষ্ম রক্তনালিগুলোতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং শরীরের সেই স্থানগুলোতে তীব্র ব্যথা অনুভূত হয়। এই রক্তকণিকাগুলো যত দ্রুত ভেঙে যায়, তত দ্রুত লোহিত রক্তকণিকা তৈরি হয় না বলে শরীরে রক্তশূন্যতা দেখা দেয়।
২. হানটিংটনস রোগ (Huntington's Disease) : এ রোগটিও হয় পয়েন্ট মিউটেশনের কারণে। এই রোগে মস্তিষ্ক ঠিকমতো কাজ করে না। শরীরের পেশিগুলোর মধ্যে সমন্বয় করার ক্ষমতা লোপ পায় এবং পরবর্তীতে মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে মৃত্যু ঘটে। এ রোগটির লক্ষণ আক্রান্ত ব্যক্তির বয়স চল্লিশ হওয়ার আগে প্রকাশ পায় না। মায়োসিস কোষ বিভাজনের সময় অ্যানাফেজ ধাপে হোমোলোগাস ক্রোমোজোমগুলোর যেকোনো একটি জোড়ায় ক্রোমোজোম দুটির একটি অপরটি থেকে পৃথক না হয়ে দুটিই যেকোনো মেরুতে চলে যায়। এ অবস্থাকে নন-ডিসজাংশন বলে। যেকোনো একটি বিশেষ ক্রোমোজোমের নন-ডিসজাংশন ঘটলে একসাথে বেশ কতগুলো লক্ষণ দেখা দেয়, তাকে সিনড্রোম বলে।
৩. ডাউন'স সিনড্রোম (Down's Syndrome) : মানুষের ২১তম ক্রোমোজোমের নন-ডিসজাংশনের ফলে এ রোগ হয়। সে কারণে ডাইন'স সিনড্রোমের মানুষে দুটির বদলে তিনটি ২১ নম্বর ক্রোমোজম থাকে। এদের চোখের পাতা ফুলা, নাক চ্যাপ্টা, জিহ্বা লম্বা এবং হাতগুলো তুলনামূলকভাবে ছোট হয়। এরা হাসিখুশি প্রকৃতির খর্বাকৃতির এবং এদের মানসিক পরিপক্বতা কম হয় ।
৪. ক্লিনিফেলটার'স সিনড্রোম (Klinefelter's Sysndrome) : এ রোগটি পুরুষ মানুষে সেক্স ক্রোমোজোমের ডিসজাংশনের কারণে সৃষ্টি হয়। ফলে পুরুষটির কোষে XY ক্রোমোজোম ছাড়াও অতিরিক্ত আর একটি X ক্রোমোজোম সংযুক্ত হয় এবং পুরুষটি হয় XXY ক্রোমোজোম বিশিষ্ট। ক্লিনিফেলটারস সিনড্রম বিশিষ্ট বালকদের মধ্যে একজন স্বাভাবিক পুরুষের যে বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যগুলো থাকা দরকার তা থাকে না। এদের কণ্ঠস্বর খুব কর্কশ হয় এবং স্তনগুলো আকারে বড় হয়। এদের বৃদ্ধি কম থাকে এবং এরা বন্ধ্যা হয়।
৫. টার্নার'স সিনড্রোম (Turner's Syndrome) : এ রোগটি নারীদের সেক্স ক্রোমোজোমের নন- ডিসজাংশনের কারণে হয় এবং স্ত্রীলোকটি হয় XX -এর পরিবর্তে শুধু একটি X ক্রোমোজোম-বিশিষ্ট । এ ধরনের স্ত্রীলোক খর্বাকৃতি হয় এবং এদের ঘাড় প্রশস্ত হয়। পূর্ণবয়স্ক অবস্থায় এদের স্তন ও জনন অঙ্গের বিকাশ ঘটে না। যার কারণে এরা বন্ধ্যা হয়। পুরুষ মানুষের সেক্স ক্রোমোজোম (X এবং Y) ছাড়া মানুষের অন্য সবগুলো ক্রোমোজোম দুটি করে আছে (হোমোলোগাস), যার অর্থ প্রত্যেকটা জিনও দুটি করে আছে। কাজেই কোনো একটি ক্রোমোজোমের কোনো একটি জিনে সমস্যা থাকলে, অন্য ক্রোমোজোমের সেই জিনটি সাধারণত দায়িত্ব নেয় বলে সমস্যাটি প্রকাশ পায় না। সমস্যাটি যদি x ক্রোমোজোমের কোনো একটি জিনে ঘটে থাকে তাহলে নারীদের দ্বিতীয় X ক্রোমোজোমের জিনটি সেই সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারে। কিন্তু পুরুষ মানুষের যেহেতু একটি মাত্র X ক্রোমোজম তাই সমস্যাটি x ক্রোমোজোমে হলে তার দ্বিতীয় কোনো পথ খোলা থাকে না। তাই X ক্রোমোজোম-সংক্রান্ত রোগগুলো পুরুষ মানুষের বেলায় অনেক বেশি হয়। একইভাবে বলা যায় Y ক্রোমোজোমের কোনো জিনে সমস্যা থাকলে সেটি শুধু পুরুষ মানুষের সমস্যা এবং দ্বিতীয় কোনো জিন না থাকায় সেটিও তারা কাটিয়ে উঠতে পারে না। প্রত্যেকটি জিনের দুটি করে কপি থাকে, তার মাঝে যেটি, তার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে সেটিকে প্রকট (Dominant) জিন বলে। যেটি তার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে না, সেটিকে প্রচ্ছন্ন (Recessive) জিন বলে। আবার যদি দুটি জিনই একই সাথে প্রচ্ছন্ন কিংবা একই সাথে প্রকট হয়, তখন তাকে হোমোজাইগাস বলে। যদি একটি প্রচ্ছন্ন অন্যটি প্রকট হয়, তখন তাকে হেটারোজাইগাস বলে। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টা সহজে বোঝা যাবে। x ক্রোমোজোমের জিন-সংক্রান্ত একটি রোগের নাম হেমোফিলিয়া এবং এটি প্রচ্ছন্ন জিন। কাজেই কন্যাসন্তানের বেলায় একটি x ক্রোমোজোমের হেমোফিলিয়া জিন থাকলেও অন্য x ক্রোমোজোমের সুস্থ জিনটি প্রকট হবে বলে হেমোফিলিয়া রোগটি প্রকাশিত হবে না। নিজের ভেতর রোগটি প্রকাশিত না হলেও এই কন্যা সন্তান রোগের বাহক হবে। কন্যাসন্তানের হেমোফিলিয়া রোগ হতে হলে তার দুটি এক্স ক্রোমোজোমেই হেমোফিলিয়ার জিন আসতে হবে। কিন্তু পুত্রসন্তানের বেলায় একটি হেমোফিলিয়ার জিন এলেই তার রোগটি প্রকাশিত হবে, কাজেই ছেলেদের বেলায় অনেক বেশি হেমোফিলিয়ার রোগ দেখা যায়।
প্রচারের কারণে জীবপ্রযুক্তি বিষয়টা বর্তমানে আমাদের কাছে খুব পরিচিত। কিন্তু বাস্তবে এর প্রয়োগ শুরু হয় অনেক আগে থেকে। সভ্যতার বিকাশের ধারাবাহিকতায় মানুষ যখন যাযাবর জীবন ছেড়ে স্থায়ী জীবনযাপন শুরু করে, তখন থেকেই জীবপ্রযুক্তির উৎপত্তি। কারণ, মানুষের কাছে তখনই অধিক ফলনশীল গাছপালা এবং শক্ত-সমর্থ প্রাণিকুল গুরুত্ব পেয়েছে। পছন্দসই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে মানুষ তখনই গাছপালা আর প্রাণী বেছে নিতে শুরু করে এবং শুরু হয় জীবপ্রযুক্তির যাত্রা। অনেক আগে থেকে মানুষ অণুজীব বা ব্যাকটেরিয়াকে কাজে লাগিয়ে দই, মদ, বিয়ার, সিরকা, পাউরুটি— এসব উৎপাদন করে এসেছে। এরপর থেকে বিভিন্ন অণুজীবের জৈবিক কর্মকাণ্ডকে কাজে লাগিয়ে শিল্প ক্ষেত্রে এবং মানবকল্যাণে নতুন নতুন উৎপাদন পৃথিবীর জীবপ্রযুক্তির ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। জীবপ্রযুক্তির সাথে সম্পর্কযুক্ত গবেষণা জীববিজ্ঞানে নতুন নতুন দিক উন্মোচিত করছে। জীবপ্রযুক্তিকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন মানবকল্যাণে প্রয়োগের জন্য জীবকে ব্যবহার করে বিভিন্ন উপাদান তৈরির প্রযুক্তিকে জীবপ্রযুক্তি বলা হয়। আমেরিকার National Science Foundation- এর দেওয়া সংজ্ঞানুযায়ী জীবপ্রযুক্তি বলতে বুঝায় মানকল্যাণের উদ্দেশ্যে জীব প্রতিনিধিদের (যেমন: অণুজীব বা জীবকোষের) কোষীয় উৎপাদনের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার। যদিও দই, সিরকা, পাউরুটি, মদ, পনির ইত্যাদি উৎপাদন জীবপ্রযুক্তির ফসল কিন্তু এসব জীবপ্রযুক্তিকে পুরোনো জীবপ্রযুক্তি বলে আখ্যায়িত করা হয়। সম্প্রতি আণবিক জীববিজ্ঞানের গবেষণার মাধ্যমে জীবপ্রযুক্তির যে প্রসার ঘটেছে, তাকে বলা হয় নতুন বা আধুনিক জীব প্রযুক্তি। বাস্তবিক অর্থে আধুনিক জীবপ্রযুক্তি তিনটি বিষয়ের সমন্বয়। যথা:
১. অণুজীব বিজ্ঞান
২. টিস্যু কালচার
৩. জিন প্রকৌশল
তাই জীবপ্রযুক্তি হচ্ছে একটি সমন্বিত বিজ্ঞান। বর্ণিত তিনটি বিষয়ের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা জীববিজ্ঞানের অত্যধুনিক এই শাখাটি মানবসভ্যতার নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে।
১১.২.১ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং
বংশানুগতির উপাদানের প্রকৃতি, রাসায়নিক গঠন এবং জৈবনিক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিসমূহ আবিষ্কৃত হওয়ার পর বিজ্ঞানীরা আর একটা বিষয় নিয়ে ভাবা শুরু করলেন। তাঁরা দেখলেন, একটা জীবের সকল জিনই তার জন্য মঙ্গলজনক নয়। এ ভাবনার ফলে জন্ম নিলো জিন প্রকৌশল নামে জীববিজ্ঞানের এক নতুন শাখা। একটি জীব থেকে একটি নির্দিষ্ট জিন বহনকারী ডিএনএ খণ্ড পৃথক করে ভিন্ন একটি জীবে স্থানান্তরের কৌশলকে জিন প্রকৌশল (Genetic Engineering) বলে। আরও সহজভাবে বলতে পারি কাঙ্ক্ষিত নতুন একটি বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির জন্য কোনো জীবের ডিএনএ-র পরিবর্তন ঘটানোকে জিন প্রকৌশল বলে। এই জিন যে কৌশলগুলোর মাধ্যমে স্থানান্তর করা হয়, তাদের একত্রে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ কৌশল বলে। রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ কৌশল অবলম্বন করে একটি ডিএনএ অণুর কাঙ্ক্ষিত অংশ কেটে আলাদা করে অন্য একটি ডিএনএ অণুতে প্রতিস্থাপনের ফলে যে নতুন ডিএনএ অণুর সৃষ্টি হয়, তাকে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ বলে। রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ তৈরির প্রক্রিয়াকে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তি বা জিন ক্লোনিং বলা হয়। মানুষের অন্ত্রে বসবাস করে একধরনের ব্যাকটেরিয়া যার নাম Escherichia coli। এই ব্যাকটেরিয়ার ওপর গবেষণা করে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অধিকাংশ কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তি নিচে উল্লেখ করা ধাপগুলো (চিত্র ১১.০৮) অবলম্বন করে সম্পন্ন করা হয়:
১. প্রথমে দাতা জীব থেকে কাঙ্ক্ষিত জিনসহ ডিএনএ অণুকে পৃথক করা হয়। এরপর এই জিনের বাহক বা ক্যারিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার জন্য ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিড ডিএনএ পৃথক করা হয়।
E. coli
দুটি উৎস E. coli ও প্রাণিকোষ) থেকে DNA-র পৃথকীভবন
প্রাণিকোষ
রেস্ট্রিকশন এনজাইমের সাহায্যে উঠা DNA-কে খণ্ডিত করণ
গাঁথন প্রান্ত
কাঙ্খিত জিন
রিকম্বিনেট DNA প্লাজমিড
DNA লাইগেজের সহায়তায় উভয় © DNA-র সংযোজন এবং রিকম্বিনেট DNA সৃষ্টি
কাঙ্খিত জিন
ট্রান্সফরমেশন প্রক্রিয়ায় রিকম্বিনেট DNA প্লাজমিড-এর ব্যাকেটেরিয়ামে প্রবেশ
ব্যাকেটেরিয়ামের ক্লোনিং:
চিত্র ১১.০৮: কাঙ্খিত জিন বহনকারী ব্যাকটেরিয়া ক্লোন
প্লাজমিড হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া কোষের ক্রোমোজোমের বাইরে আরেকটি স্বতন্ত্র ডিএনএ অণু যেটি বিভাজিত হতে পারে বা শবিভাজনে সক্ষম।
২. এ ধাপে প্লাজমিড ডিএনএ এবং দাতা ডিএনএ এক বিশেষ ধরনের এনজাইম বা উৎসেচক দিয়ে খণ্ডিত করা হয়। দাতা ডিএনএর এসব খন্ডের কোনো একটিতে কাঙ্ক্ষিত জিনটি থাকে।
৩. এ ধাপে লাইগেজ নামক একধরনের এনজাইম দিয়ে দাতা ডিএনএ কে প্লাজমিড ডিএনএ এর কাটা প্রান্ত দুটোর মাঝখানে স্থাপন করা হয়। লাইগেজ এখানে আঠার মতো কাজ করে। এর ফলে নির্দিষ্ট জিনসহ রিকম্বিনেন্ট ডিএএন প্লাজমিড তৈরি হয়। এই রিকম্বিনেন্ট প্লাজমিড এখন দাতা ডিএনএ র খণ্ডিত অংশ বহন করে।
৪. এখন এই রিকম্বিনেন্ট প্লাজমিডকে ব্যাকটেরিয়ার ভেতরে প্রবেশ করানো হয়। খণ্ডিত ডিএনএ গ্রাহক কোষে প্রবেশ করনোর পদ্ধতিকে ট্রান্সফরমেশন বলে। ট্রান্সফরমেশনের ফলে নতুন জিন নিয়ে যে ব্যাকটেরিয়া বা জীবের উদ্ভব ঘটে, তাকে ট্রান্সজেনিক জীব বলে।
৫. এরপর নির্দিষ্ট জিন বহনকারী রিকম্বিনেন্ট প্লাজমিড ধারণ করা ব্যাকটেরিয়াকে শনাক্ত করে আলাদা করা হয়। এরপর নির্দিষ্ট জিন বহনকারী ব্যাকটেরিয়াগুলোর ব্যাপক বংশবৃদ্ধি ঘটানো হয়। এই ব্যাকটেরিয়াগুলোর প্রত্যেকটিতে এখন একটি করে কাঙ্ক্ষিত জিন রয়েছে। এই পদ্ধতিতে জিন তৈরি করাকে বলা হয় জিন ক্লোনিং। জিনকে ব্যবহার করার জন্য প্লাজমিডকে আবার আলাদা করে নেওয়া হয়।
১১.২.২ ক্লোনিং
প্রাকৃতিক ক্লোন বলতে একটি জীব অথবা এক দল জীবকে বোঝানো হয়, যাদের উদ্ভব ঘটে অযৌন অঙ্গজ প্রজননের দ্বারা। এগুলোর প্রকৃতি হয় পুরোপুরি তার মাতৃজীবের মতো। জীব ছাড়াও একটি কোষ বা একগুচ্ছ কোষ যখন একটিমাত্র কোষ থেকে উৎপত্তি হয় এবং সেগুলোর প্রকৃতি মাতৃকোষের মতো হয়, তখন তাকেও ক্লোন বলে। প্রকৃতিতে ব্যাকটেরিয়া, অনেক শৈবাল, বেশির ভাগ প্রোটোজোয়া এবং ইস্ট ছত্রাক ক্লোনিং পদ্ধতি দিয়ে বংশবৃদ্ধি করে। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবহার করে তিন ধরনের ক্লোনিং করা হয়।
১. জিন ক্লোনিং: একই জিনের অসংখ্য নকল তৈরি করাকে জিন ক্লোনিং বলে। জিন ক্লোনিং রিকম্বিন্যান্ট ডিএনএ টেকনোলজির সাহায্যে ঘটানো হয়।
২. সেল ক্লোনিং: একই কোষের অসংখ্য হুবহু একই রকমের কোষ সৃষ্টি করাকে সেল ক্লোনিং বলে।
৩. জীব ক্লোনিং: দুটির পরিবর্তে একটিমাত্র জীব থেকে জিনগত হুবহু এক বা একাধিক জীব তৈরির পদ্ধতিকে জীব ক্লোনিং বলে।
ডলি নামক ভেড়া হচ্ছে পৃথিবীর প্রথম স্তন্যপায়ী প্রাণী, যা একটি পূর্ণবয়স্ক দেহকোষ থেকে ক্লোন করা হয়েছে। ক্লোন করার সময় নিচের ধাপগুলো (চিত্র ১১.০৯) অনুসরণ করা হয়। এক্ষেত্রে ডিম্বাণু থেকে যে প্রাণী সৃষ্টি হয়, তা হুবুহ তার মাতার মতো হয়।
অনিষিক্ত ডিম
দাতা ভেড়া
নিউক্লিয়াস অপসারণ
নিউক্লিয়াসযুক্ত কোষের স্থানান্তর
কোষ কালচার
এবং জীনগত পরিবর্তন
পালক মায়ের শরীরে ভ্রুণ স্থানান্তর
দাতা ভেড়ার অনুরূপ জিনসহ মেষশাবক
চিত্র ১১.০৯: ডলির সৃষ্টি
১. ডলি নামক ভেড়াকে ক্লোন করার জন্য বিজ্ঞানীরা একটা ছয় বছর বয়সের সাদা ভেড়ার দুধগ্রন্থি থেকে কোষ সংগ্রহ করেছেন।
২. এই কোষের ভেতরের নিউক্লিয়াসটিকে তার কোষে “অভুক্ত” রাখা হয়েছে, যেন এটি যে দুগ্ধগ্রন্থির একটি কোষের নিউক্লিয়াস এই তথ্যটি ভুলে যায়।
৩. কালো মুখের আরেকটি ভেড়া থেকে একটি ডিম্বাণু সংগ্রহ করে তার ভেতরকার নিউক্লিয়াসটিকে অপসারণ করা হয়েছে।
৪. সাদা ভেড়া থেকে সংগ্রহ করা কোষের নিউক্লিয়াসটি এবার ডিম্বাণুতে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এবং ইলেকট্রিক শক দিয়ে নিউক্লিয়াসটিকে কার্যকর করা হয়েছে।
৫. ডিম্বাণুটি ভ্রূণে পরিণত হওয়ার পর সেটি একটা পালক মাতা ভেড়ার দেহে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। মাতা ভ্রুনটিকে যথাসময়ে মেষশাবক হিসেবে জন্ম দিয়েছে। এই মেষশাবকটি হুবহু তার মায়ের মত।
এই ক্লোনিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে ক্লোন ইঁদুর, খরগোস, গরু ও শুকর এমনকি বানর পর্যন্ত ক্লোন করা হয়েছে। ইঁদুর, ভেড়া, বানর প্রভৃতি ক্লোনিংয়ের পর স্বাভাবিকভাবেই বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি এখন মানুষের ওপর। এ প্রক্রিয়াটি এখন আর দুরূহ নয়, কিন্তু ইতোমধ্যে বিভিন্ন দেশ মানুষের ক্লোন করার প্রক্রিয়া আইন করে নিষিদ্ধ করে রেখেছে। ক্লোনিংয়ের সামাজিক প্রভাব: সম্পূর্ণ প্রাণীর ক্লোনিংকে বলে রিপ্রোডাকটিভ ক্লোনিং। 'ডলি' নামক ভেড়া তার উদাহরণ। পশুদের ক্লোনিং নিয়ে তেমন কোনো বিতর্ক সৃষ্টি হয়নি, তবে এর মধ্যে মানুষের ক্লোনিংয়ের চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে। এখন এর নৈতিকতা নিয়ে বিতর্ক উঠেছে।
নৈতিকতা প্রশ্নগুলো এরকম:
প্রথমত হচ্ছে ক্লোনিং হয়ে ভূমিষ্ঠ হওয়া শিশুটি যখন বড় হবে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, ব্যক্তিত্ব ওই ক্লোন হতে পাওয়া ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের মতো হবে, নাকি অন্যরকম হবে। দ্বিতীয় এইভাবে ক্লোন হয়ে সৃষ্টি হওয়ায় শিশুটির উপর কী কোনো ধরনের সামাজিক চাপ থাকবে? ক্লোনিং জাত শিশুটি সম্পূর্ণ সুস্থ হবে, নাকি প্রতিবন্ধী বা বিকলাঙ্গ হবে, সেটি সম্পর্কেও বিজ্ঞানীরা এখনো পুরোপুরি নিশ্চিত নন। এখন পর্যন্ত মানুষ বা মানবগোষ্ঠীর সফল ক্লোনিংয়ের খবর পাওয়া যায়নি। আরব্য উপন্যাসের সেই দৈত্যের কাহিনী আমরা জানি, যাকে বোতল থেকে বের করার পর পুনরায় বোতলে ঢোকানো যায়নি। পরমাণু শক্তির মতো জীবপ্রযুক্তি ঠিক তেমন এক অবাধ্য শক্তি। তাই আমাদের কাজ হচ্ছে, দায়িত্বশীল মানুষের মতো বিবেচনা করে মানবজাতির কল্যাণে এই জীবপ্রযুক্তিকে কাজে লাগানো।
জিন প্রকৌশল ব্যবহার করে উন্নত প্রাণী উদ্ভাবনের জন্য বিজ্ঞানীরা অনেক দিন থেকে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং কোথাও কোথাও সফলও হয়েছেন। তারই একটি ফসল হচ্ছে ট্রান্সজেনিক জীব (প্ৰাণী অথবা উদ্ভিদ)। ট্রান্সজেনিক জীব উৎপাদনের পদ্ধতিকে ট্রান্সজেনেসিস বলে। রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ ও মাইক্রোইনজেকশন কৌশল প্রয়োগ করে ট্রান্সজেনিক জীব উদ্ভাবন করা হয়।ব্যাকটেরিয়া থেকে শুরু করে উদ্ভিদ ও অনেক প্রাণীর ক্ষেত্রে ট্রান্সজেনিক জীব উৎপন্ন করা সম্ভব হয়েছে। ফলে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং দিয়ে উদ্ভাবিত ট্রান্সজেনিক জীব পৃথিবীতে একটি নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে এবং গৃহপালিত পশুদের উন্নতিসাধনে ট্রান্সজেনেসিস সহজভাবে আমাদের সাফল্য বয়ে এনেছে।ট্রান্সজেনিক প্রাণী: মানুষের জিন বিশেষ পদ্ধতিতে ইঁদুরে প্রবেশ করিয়ে এমন ট্রান্সজেনিক ইঁদুর উৎপাদন সম্ভব হয়েছে, যা মানুষের অ্যান্টিবডিগুলো তৈরি করতে সক্ষম। একই পদ্ধতিতে ট্রান্সজেনিক গবাদিপশু, ভেড়া, ছাগল, শুকর, পাখি ও মাছ উৎপাদন করা হয়েছে। ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ: জিন প্রকৌশলের মাধ্যমে জিনের স্থানান্তর ঘটিয়ে যেসব উদ্ভিদ সৃষ্টি করা হয়, সেগুলোকে ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ বলে। রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ কৌশল প্রয়োগ করে একটি কাঙ্ক্ষিত জিন উদ্ভিদদেহের কোষের প্রোটোপ্লাজমে প্রবেশ করানো হয়।গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থকরী ফসলকে ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদে পরিণত করে পতঙ্গ, ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক প্রতিরোধী করে উৎপাদন করা হচ্ছে। শৈত্য, লবণাক্ততা, খরা, নাইট্রোজেন ও ফাইটোহরমোন স্বল্পতা ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ উদ্ভাবন করে মোকাবিলা করা সক্ষম হয়েছে। বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রায় ৬০টির মতো উদ্ভিদ প্রজাতিতে এ প্রক্রিয়ার সফল প্রয়োগ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে: টমেটো, তামাক, আলু, লেটুস, বাঁধাকপি, সয়াবিন, সূর্যমুখী, শসা, তুলা, মটর, গাজর, আপেল, মুলা, পেঁপে, ধান, গম, ভুট্টা ইত্যাদি। টান্সজেনিক টমেটো উদ্ভাবন করে পাকা টমেটোর ত্বক নরম হওয়া প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, এগুলোকে বিলম্বে পাকানো এবং এর ভেতর সুক্রোজের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
১১.৩.১ কৃষি উন্নয়নে জীবপ্রযুক্তির ব্যবহার
মানুষের অন্যতম প্রধান মৌলিক চাহিদা খাদ্য। কিন্তু সীমিত ভূখণ্ডে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা নিয়ে কীভাবে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া যায় কিংবা কীভাবে উদ্বৃত্ত খাদ্য উৎপাদন করে ব্যবসায়িক ফায়দা ওঠানো যায়, সেটি নিয়ে সারা পৃথিবীতে চলছে এক অঘোষিত যুদ্ধ। এ যুদ্ধ জয়ের হাতিয়ার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে সফল জীবপ্রযুক্তির প্রয়োগ।
কৃষি উন্নয়নে যেসব জীবপ্রযুক্তিগত পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়, সেগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো:
১. টিস্যু কালচার: এ পদ্ধতিতে উদ্ভিদের বর্ধনশীল অঙ্গের ক্ষুদ্র অংশ; যেমন মূল, কাণ্ড, পাতা, অঙ্কুতির চারার বিভিন্ন অংশ ইত্যাদি নির্ধারিত আবাদ মাধ্যমে জীবাণুমুক্ত ও নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে আবাদ করা হয়। এই কালচারের ফলে এসব বর্ধনশীল অঙ্গসমূহ থেকে অসংখ্য অণুচারা উৎপন্ন হয়। এসব অণুচারার প্রত্যেকটি পরে উপযুক্ত পরিবেশে পৃথক পৃথক পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদে পরিণত হয়। এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে অল্প জায়গায় নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে বাণিজ্যিকভাবে লাখ লাখ কাঙ্ক্ষিত চারা তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে।
২. অধিক ফলনশীল উদ্ভিদের জাত সৃষ্টি: কোনো বন্য উদ্ভিদের উৎকৃষ্ট জিন ফসলি উদ্ভিদে প্রতিস্থাপন করে কিংবা জিনের গঠন বা বিন্যাসের পরিবর্তন ঘটিয়ে উন্নত জাতের উদ্ভিদ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। এভাবে ধান, গম, তেলবীজসহ অনেক শস্যের অধিক ফলনশীল উন্নত জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে।
৩. গুণগত মান উন্নয়নে: জীবপ্রযুক্তি প্রয়োগ করে প্রাণী ও উদ্ভিদজাত দ্রব্যাদির গঠন, বর্ণ, পুষ্টিগুণ, স্বাদ ইত্যাদির উন্নয়ন করা সম্ভব হয়েছে। যেমন: অস্ট্রেলিয়ায় ভেড়ার লোমকে উন্নতমানের করতে তাদের খাদ্য ক্লোভার ঘাসে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তির মাধ্যমে সূর্যমুখীর সালফার অ্যামিনো অ্যাসিড সৃষ্টিকারী জিন স্থানান্তর করা হয়েছে। ফলে খাদ্য হিসেবে এই ঘাস খেলেই ভেড়ার লোম উন্নতমানের হচ্ছে, পৃথকভাবে সালফার সমৃদ্ধ খাবার দেওয়া প্রয়োজন হচ্ছে না ।
৪. সুপার রাইস সৃষ্টি: জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে সুইডেনের এক বিজ্ঞানী সুপার রাইস বা গোল্ডেন রাইস নামক এক ধরনের ধান উদ্ভাবন করেছেন। এটি ভিটামিন A সমৃদ্ধ ।
৫. ভিটামিন সমৃদ্ধ ভুট্টার জাত সৃষ্টি: সম্প্রতি স্পেনের একদল গবেষক জেনেটিক্যালি মডিফাইড ভুট্টার বীজ উদ্ভাবন করেছেন যাতে ভিটামিন সি, বিটা ক্যারোটিন ও ফলিক অ্যাসিড পাওয়া যাবে। এই ভুট্টা ব্যালেন্স ডায়েটের পাশাপাশি গরিব দেশগুলোর মানুষের অপুষ্টি দূর করবে।
৬. স্টেরাইল ইনসেক্ট টেকনিক: জীবপ্রযুক্তি দিয়ে শাক-সবজি, ফল ও শুঁটকির ক্ষতিকর পতঙ্গ, মশা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণে স্টেরাইল ইনসেক্ট টেকনিকট (SIT) উদ্ভাবন করা হয়েছে। এটি ব্যবহার করে পতঙ্গের বংশবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। জাপান, ফিলিপিনস, থাইল্যান্ড, গুয়াতেমালা, ব্রাজিল এসব দেশে এই প্রযুক্তি ব্যাপক প্রচলিত।
৭. ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ: এ সময় পর্যন্ত প্রায় ৬০টি উদ্ভিদ প্রজাতিতে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ কৌশল সফলভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে তামাক, টমেটো, আলু, মিষ্টি আলু, লেটুস, সূর্যমুখী, বাঁধাকপি, তুলা, সয়াবিন, মটর, শসা, গাজর, মুলা, পেঁপে, আঙ্গুর, কৃষ্ণচূড়া, গোলাপ, নাশপাতি, নিম, ধান, গম, রাই, ভুট্টা প্রভৃতি। এগুলো পতঙ্গ, ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক প্রতিরোধী এবং একই সাথে যেকোনো পরিবেশকে মোকাবিলা করতে পারে।
১১.৩.২ ঔষধশিল্পে জীবপ্রযুক্তির ব্যবহার
প্রতিবছর জনসংখ্যা ও রোগের জটিলতা বেড়েই চলছে। এ অবস্থায় দ্রুত চিকিৎসা পৌঁছে দিতে বিজ্ঞানীরা জীবপ্রযুক্তি ব্যবহার করে ঔষধশিল্পের উন্নতি ঘটিয়েছেন। মারাত্মক রোগ-ব্যাধি শনাক্তকরণের পাশাপাশি জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে ঔষধ উৎপাদনের প্রক্রিয়া জোরালো হয়েছে। নিচে তার কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো।
১. ভ্যাকসিন উৎপাদন: বর্তমানে জিন প্রকৌশল প্রযুক্তি প্রয়োগ করে ব্যাপকভাবে বিভিন্ন ভ্যাকসিন বা টিকা উৎপাদন করা হয়েছে যেগুলো পোলিও, যক্ষ্মা, হাম, বসন্তসহ বিভিন্ন সংক্রামক রোগের রোগ প্রতিরোধক হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।
২. ইন্টারফেরন উৎপাদন: ইন্টারফেরন আধুনিক ঔষধশিল্পে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রোটিন অণুর সমন্বয়ে গঠিত এ উপাদানটি দেহের রোগের প্রতিরোধ ব্যবস্থায় অত্যন্ত সহায়ক। জিন প্রকৌশল প্রয়োগ করে বাণিজ্যিক ভিত্তিক ইন্টারফেরন উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। এটি হেপাটাইটিসের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয় এবং ক্যান্সার রোগীদেরকে প্রাথমিকভাবে ইন্টারফেরন প্রয়োগ করে ক্যান্সারকে নিয়ন্ত্রণে রাখার পদক্ষেপ নেওয়া হয়।
৩. হরমোন উৎপাদন: বিভিন্ন হরমোন (যেমন: ডায়াবেটিস রোগের ইনসুলিন কিংবা মানুষের দেহ বৃদ্ধির হরমোন ইত্যাদি) উৎপাদন জীবপ্রযুক্তির এটি উল্লেখযোগ্য দিক। জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে প্রস্তুত করা হরমোন সহজসাধ্য এবং দামও অনেক কম।
৪. অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদন : কম সময়ের মধ্যে বিপুল পরিমাণ অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদনের জন্য জীবপ্রযুক্তির প্রয়োগ করে বর্তমানে এক হাজারের বেশি অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদিত হচ্ছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে পেনিসিলিন ও সেফালোস্পোরিন অ্যান্টিবায়োটিক।
৫. এনজাইম উৎপাদন: পরিপাক-সংক্রান্ত রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত ওষুধের উপাদান হিসেবে কিছু এনজাইম, (যেমন: অ্যামাইলেজ, প্রোটিয়েজ ও লাইপেজ, পেঁপে থেকে প্যাপেইন) প্রস্তুত করা হয়। বটগাছ থেকে ফাইসন (যা কৃমিরোগে ব্যবহৃত হয়), গবাদিপশুর প্লাজমা থেকে থ্রম্বিন (রক্তপাত বন্ধে ব্যবহৃত হয়) এবং ট্রিপসিন (যা ক্ষত নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়) জৈবপ্রযুক্তি ব্যবহার করে উৎপাদিত এবং বাজারজাত হচ্ছে।
৬. ট্রান্সজেনিক প্রাণী থেকে ঔষধ আহরণ: ট্রান্সজেনিক প্রাণী উদ্ভাবনের মাধ্যমে প্রাণীগুলোর দুধ, রক্ত ও মূত্র থেকে প্রয়োজনীয় ঔষধ আহরণ করা হয়। একে মলিকুলার ফার্মিং বলে।
১১.৩.৩ গৃহপালিত পশু উন্নয়নে জীবপ্রযুক্তির ব্যবহার:
উন্নত জাতের পশু উৎপাদনের লক্ষ্য হচ্ছে: (ক) চর্বিমুক্ত মাংস উৎপাদন, (খ) দ্রুত বিক্রয়যোগ্য করা এবং (গ) রোগ প্রতিরোধী করা। ইতোমধ্যে ট্রান্সজেনিক ভেড়া উদ্ভাবন করা হয়েছে। এই ভেড়ার প্রতি লিটার দুধে ৩৫ গ্রাম পর্যন্ত হিউম্যান আলফা এন্টিট্রিপসিন প্রোটিন পাওয়া যায়। এ প্রোটিনের অভাবে এমফাইসেমা নামক মারাত্মক রোগের সৃষ্টি হয়। জিন প্রযুক্তির মাধ্যমে ভেড়াদেহের মাংস বৃদ্ধি এবং শরীরের পশম-বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা হয়েছে। চর্বিহীন মাংস ও মানুষের হরমোন উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ট্রান্সজেনিক শূকর উদ্ভাবন সফল হয়েছে। উদ্ভাবিত হয়েছে ট্রান্সজেনিক ছাগল। এসব ছাগলের দুধে পাওয়া যায় এক বিশেষ ধরনের প্রোটিন যা জমাট রক্তকে গলিয়ে করোনারি প্রন্থোসিস থেকে মানুষকে রক্ষা করে। ট্রান্সজেনিক গরু উদ্ভাবনের মাধ্যমে মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের মাতৃদুধের অতি প্রয়োজনীয় প্রোটিন, ল্যাকটোফেরিনও পাওয়া যাচ্ছে। দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদনে জিন প্রযুক্তির ব্যবহার: বিশ্বে দুধের প্রধান উৎস পাভী। এর পরেই রয়েছে মহিষ, ছাগল ও ভেড়া। দুধের সরাসরি নানাবিধ ব্যবহার থাকলেও দুখ থেকে বিভিন্ন প্রযুক্তির মাধ্যমে দুখত দ্রব্যাদি তৈরি করা হয়। যেমন: মুখ থেকে মাখন, পনির, দই ইত্যাদি খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করা হয়। দুখ থেকে খাদ্যসামগ্রী তৈরির জন্য জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে নানা রকমের ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার করা হচ্ছে।
নিচে কয়েকটি দুগ্ধজাত দ্রব্য তৈরি সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।
১. মাখন: বিশেষ ব্যাকটেরিয়া থেকে উৎপন্ন এনজাইম দিয়ে মাখনে বিশেষ সুগন্ধ ও স্বাদ সৃষ্টি করা হয়।
২. পনির: আমাদের দেশে গরুর দুধ কিংবা মহিষের দুধ থেকে পনির তৈরি করা হয়। পনির তৈরিতে ব্যাকটেরিয়া কিংবা ছত্রাক প্রয়োগ করা হয়। এতে পনিরের স্বাদ, বর্ণ এবং গন্থের তারতম্য ঘটে। পৃথিবীর সুস্বাদু পনির উৎপাদনের জন্য ইতালি, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ড ও যুক্তরাজ্য বিখ্যাত। এই উৎকৃষ্ট মানের পনির উৎপাদন সম্ভব হয়েছে জীব প্রযুক্তির দ্বারা।
৩. দই: দুধে ল্যাকটোজ নামক শর্করা থাকায় বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া প্রয়োগ করে সেটা থেকে দই বা দইজাতীয় খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করা যায়। ল্যাকটিক অ্যাসিড ব্যাকটেরিয়া দুধের জমাট বাঁধা অবস্থা সৃষ্টি করে দইয়ে রূপান্তরিত করে। এটি করার জন্য ল্যান্টিক অ্যাসিড ব্যাকটেরিয়া নামে এক প্রকার ব্যাকটেরিয়ার বীজ ব্যবহার করা হয়। মূলত এর গুণাগুণের ওপরেই দই এর গুণাগুণ নির্ভর করে।
১১.৩.৪ ফরেনসিক টেস্ট
ফরেনসিক টেস্টের দ্বারা রন্তু, বীর্যরস, মূত্র, অশ্রু, লালা ইত্যাদির ডিএনএ অথবা অ্যান্টিবডি থেকে অপরাধীকে শান্ত করা সম্ভব হয়। জীবপ্রযুক্তি প্রয়োগ করে ফরেনসিক টেস্ট (চিত্র ১১.১০) করার পদ্ধতি এরকম: সেরোলজি (Serology) টেস্ট দিয়ে মানুষের রক্ত, বীর্ষ এবং লালাকে চিহ্নিত করে তার ডিএনএ বিশ্লেষণ করে অপরাধীকে শনাক্ত করা হয়। আমরা এ পর্যন্ত জিন প্রকৌশলের প্রয়োগ ও অবদান সম্পর্কে যেসব আলোচনা করেছি, এগুলো ছাড়াও আরও অনেক ধরনের কাজ হয়েছে। জিন প্রকৌশল প্রযুক্তি ব্যবহার করে "হিউম্যান জিনোম প্রজেক্ট" -এর মাধ্যমে বিভিন্ন ক্রোমোজোমে অবস্থিত জিনগুলোর অবস্থান ও কাজ সম্বন্ধে জানা সম্ভব হয়েছে। এর ফলে মানুষের শরীরের ক্ষতিকর জিনকে অপসারণ করে সুস্থ জিন প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হতে যাচ্ছে। এই পদ্ধতিকে জিন থেরাপি বলে।